
হারানো সূত্র
শাহীনুর ইসলাম
ব্যালকোনির চেয়ারে বসে আছে অনিক বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাতে রাখা ম্যাগাজিনটার প্রচ্ছদ পাতায়। কিন্তু সে দেখছে অন্য কিছু। কারণ মন যখন একাই দেখে, চোখ তখন দেখেও দেখে না। এ অবস্থায় মানুষ দেখে অতীত ও ভবিষ্যৎ, যার মধ্যে অতীতটাই ঘাড়ে চেপে বসে বেশি। বর্তমানকে দেখতে হলে চোখ ও মন দুটোরই সংযোগ লাগে। সেই সংযোগ ঘটানোর ক্ষমতা সুস্থ মানুষ মাত্রেরই থাকে। কিন্তু অনিকের সে ক্ষমতাটা হারিয়ে গেছে এই মুহূর্তে। তাই ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রেখে ঘুরছে অতীতের অলি-গলি।
সেই ছোটবেলায় জন্মভূমিতে থাকতে কার কাছ থেকে যেন শুনেছিল ঘোড়ার ডিম পাওয়া যায়। বাসায় এসে বাবার কাছে বায়না ধরে— তাকে ঘোড়ার ডিম এনে দিতে হবে। মুরগীর ডিম খেতে তার আর ভাল লাগে না। তাছাড়া মুরগীর ডিম, হাঁসের ডিম, এমনকি বক-ঘুঘু-কবুতরসহ কিছু পাখির ডিমও সে আগে খেয়েছে। কিন্তু ঘোড়ার ডিম কখনো দেখেনি। খাওয়া তো দূরের কথা। না জানি কত মজার!
বাবা তো তাকে মিথ্যে বলতে পারতেন না। তাই তাকে অনেক করে বুঝিয়েছিলেন যে, পাখির ডিম হয়, মুরগীর ডিম হয়, হাসের ডিম হয়, সাপের ডিম হয়, কীটপতঙ্গেরও ডিম হয়। কিন্তু ঘোড়ার ডিম হয় না। মানুষ ও অন্যান্য পশুর মতোই ঘোড়াও বাচ্চা প্রসব করে। এত বোঝানোর পরও অনিক কিছুতেই বুঝতে চাইছিল না। তার মনে হয়েছিল বাবা তাকে ঘোড়ার ডিম কিনে দেবে না। তাই এটা সেটা বলে এড়াতে চাইছে। খুব করে জিদ ধরেছিল সেদিন। পরে বাধ্য হয়ে বাবা তাকে খেলনা ধরনের বড় একটা ডিম এনে দেওয়ার পরই কেবল ক্ষান্ত হয় সে। স্মৃতির এ ঘটনা মনে করে তার ঠোঁটের কোণাটা হাসির ঝিলিকের মতো করে একটু নড়ে ওঠে।
কিন্তু ক্রন্দন সমুদ্রের জোয়ার আবার উতলে ওঠে। দুষ্টামিভরা স্মৃতিগুলো মনে পড়তেই সে জোয়ারে একটু বিরতি পড়ে মাত্র। বেশিরভাগ স্মৃতিই ছবির মানুষটাকে অযথা নির্যাতন করার স্মৃতি। স্মৃতির টুকরো অংশগুলো থেকে ফিরে আসতেই আফসোস হয় তার সাথে সে এগুলো না করলেও পারত। তখন যদি একটু জ্ঞান থাকত!
প্রতিটা আফসোস যেন একেকটা নদী হয়ে সাগরের সাথে মিশে যাচ্ছে। তাই সাগরের প্রবাহ অতিমাত্রায় বাড়ছে। প্রতিটা আফসোসের ধাক্কাও লাগছে সাগরের পানিতে। তবে হাতের ম্যাগাজিনটি তাকে বড় ধাক্কা দিয়ে জলোচ্ছ্বাসের কবলে ফেলে দিয়েছে এবার। এটা তার বুক ছাপিয়ে চোখের উপকূলকে উত্তাল ঢেউয়ে ভিজিয়ে যায়। মনের অজান্তেই হাতে রাখা ম্যাগাজিনটার উপর টপটপ করে পানি পড়ে। তারই দু’ফোঁটা ছবিটার উপর টুপ করে পড়তেই যেন একটু হুঁশ হয় তার।
বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল কিনা যাচাই করতে আকাশের দিকে তাকায়। কোথাও মেঘের ঘনঘটা নেই। নিজের দিকে ফিরে আসে। সজ্ঞানে অনুভব করে চোখের সাগর থেকে গাল বেয়ে নোনা জল পড়ার ভেজা আঁঠালো ভাব। এবার চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে। উপরে যেদিকটায় সাগর প্রবাহ পৌঁছাতে পারবে না ম্যাগাজিনটা একটু সাবধানে ও নিরাপদে সেদিকে তুলে ধরে । কারণ নিজের অশ্রু ঝরার চেয়েও ম্যাগাজিনের এই পাতাটা এখন বেশি মূল্যবান তার কাছে।
ছবির ঠিক উপরের দিকে খেয়াল করে দুটো শব্দ যেখানে রয়েছে ছয়টি অক্ষর। শব্দ দুটোর আকার-আকৃতি বলে দিচ্ছে এটা ছবির মানুষটারই নাম হবে। এ নাম অনিকের অনেক চেনা। জন্মের আগ থেকেই এ নামের সাথে তার ওঠা-বসা। বিশেষ করে এ নামের উচ্চারণের সাথে।
হঠাৎ বাতাসে একটা সুর ভাসে মৃদু শব্দে। যেন রাতের আকাশে মনোযোগ দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখার সময় একটা উল্কা হুট করেই জ্বলে জ্বলে খসে পড়ছে। সুরটা কয়েক সেকেন্ড শোনার পর অবাক হয় সে। ভাল করে কান পাততেই সেটা বেশ চেনা লাগে তার কাছে। ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার ‘পরে ঠেকাই মাথা’। এ গানটা তার বাবা প্রায়শই শুনত এবং মাঝে মাঝে গুন গুন করত। বাবার বদৌলতে উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু দুটো বাংলা গান এখন জানে সে। অন্য গানটি ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’।
কিন্তু এ গান তো শীতের এ দেশে বেজে ওঠার কথা নয়। এখানকার খোলা বাতাসে ধ্বনিত হবে ইংরেজি বা ফরাসি সঙ্গীত। আরেকটু মনোযোগ দিয়ে উৎস খুঁজতেই সে আবিস্কার করে, তার নিজের প্যান্টের পকেট থেকেই গানটা বাজছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে দেখে সত্যি তা-ই। বাবার প্রিয় এ গানটা সে মাত্র তিনদিন আগে মুঠোফোনে নামিয়ে রেখে দিয়েছে। এখন পকেটে চাপ পড়ে কীভাবে যেন ঠিক এ গানটাই বেজে উঠেছে।
গানটা বন্ধ করে মুঠোফোনটা আবার পকেটে রেখে দেয় অনিক। এরপর ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ পাতাটা উল্টিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। লক্ষ করে লেখার লাইনগুলো সমান্তরাল রেখা তৈরী করেছে। তিনটা কলাম আছে। কলামের প্রতিটা লাইনের উপরে একটা রেখার মতো আছে। তবে ভাঙ্গা রেখা। এ রেখাই কল্পিত সমান্তরাল রেখা তৈরী করেছে। প্রতিটা লাইনই এমন। আদর করে পৃষ্ঠাটির লাইনগুলোর উপর আঙ্গুল বুলিয়ে যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এভাবে পর পর তিনটা পৃষ্টা ভ্রমণ করে আবার ঘুরে এসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছবিটাতে। ছবিটাই তাকে কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। লেখাগুলো শুধুই ক্লান্ত করে যাচ্ছে। তাই উল্টে-পাল্টে প্রচ্ছদের ছবিটার কাছে ফিরে আসে সে।
কী এক অপরিসীম মায়া ঝরে পড়ছে ছবিটা থেকে! জীবন্ত দৃষ্টি। হাসিমাখা মুখ। কে বলবে ইনি এখন শুধুই প্রচ্ছদপটের ছবি?
কিছুক্ষণ পর উদাস দৃষ্টিতে শূন্যে তাকায়। শূন্যও তাকে আশ্রয় দেয় না। স্বস্তিও দেয় না। ফিরে ফিরে ছবিটার মধ্যে তাই প্রশ্রয় খোঁজে। কত কথা বলে যাচ্ছে ছবিটার সাথে!
আবার ভেতরের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে অন্যান্য লেখার উপর আঙ্গুলের মায়াময় স্পর্শ দেয়। দিতে দিতে ভাবে— এখানকার সব লেখাই সম্ভবত তাকে নিয়ে। সম্পাদক সাহেব তো তেমনটাই বলেছিলেন।
প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে গিয়ে সে খেয়াল করে প্রচ্ছদ পাতার নামটার মতো এখানেও ছয় অক্ষরের একই আকৃতির দুটি শব্দ। তবে ছোট আকারে। ধরেই নেয় এটাই ছবির মানুষটির লেখা। এখানে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সিক্ত অনুমিত অবলম্বনের নিবিড় পরশ বুলিয়ে যায় সে। বুকে জড়িয়ে ধরে; ঠোঁটে নিয়ে চুমুও খায়। মনে মনে ভাবে—আর কখনো সাক্ষাৎ কথা হবে না। কথা যা হবে তা কল্পনায় স্মৃতির সাথে। তার লেখাগুলোর সাথে জীবন্ত যোগাযোগ হতে পারত। কিন্তু তাও আর সম্ভব নয়।
এখন তার হাতের কাছেই তিনি কত কী বলে যাচ্ছেন! এখন থেকে আমরণ তার সাথে শুধু এভাবেই কথা বলে যাবেন। কিন্তু কিছুই তার বুঝতে পারছে না সে। অস্পষ্ট হাতের লেখা হলে এক কথা ছিল। কিংবা লেখাপড়া না জানলে নয় মানা যেত যে পড়তে পারছে না। সে উচ্চশিক্ষিত ছেলে। সরকারি চাকুরিও করে। বিদেশের মাটিতে অনেক বাবা-মায়েই পারে না এমন করে শিক্ষিত করে তুলতে নিতান্তই নিজের আগ্রহ ছাড়া। কারণ এখানকার শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া কিংবা জোর জবরদস্তি করা আইনবহির্ভূত। সেখানে তার বাবা-মা তাকে যথেষ্ট উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছে। এত কিছু সত্ত্বেও লেখাগুলো এখন পড়তে পারছে না সে। আগে কখনো প্রয়োজন বোধ করেনি মানুষটির লেখাগুলো পড়ার। আজ যখন অত্যন্ত প্রয়োজন, তখন সেই ক্ষমতা ও দক্ষতা তার ঝুলিতে নেই।
না, তার চোখে এখনো চশমা ওঠেনি। চল্লিশ পেরোল গত বছর। অন্ধ তো নয়-ই। কিছু পড়ার সময় মনোসংযোগ করার ক্ষমতাও রাখে যথেষ্ট। তাদের ঘরে দু’শোর মতো বই আছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনসহ নানা শাস্ত্রের বই। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু জার্নাল এবং ম্যাগাজিনও সংগ্রহে আছে। যেগুলোর বেশির ভাগই ইংরেজিতে লেখা। বাংলায় শুধু কিছু বই আছে। তার মধ্যে ছবির মানুষটিরই লেখা আছে বাংলায় লেখা দশটি বই। আর তিনটা জার্নালে তিনটা লেখা আছে ইংরেজিতে।
জার্নালের গবেষণাধর্মী লেখাগুলো অনিক কখনো পড়েনি। কারণ এর বিষয়বস্তু তার আগ্রহের বিষয় ছিল না কখনো। শুধু শিরোনাম পড়ে রেখে দিয়েছিল। আর যে বইগুলোতে মানুষটির নিজের জীবনের বেড়া ওঠার ইতিহাস, চিন্তা-ভাবনা, জীবনবোধ, জগৎপাঠ ও দৃষ্টিভঙ্গি মলাটবদ্ধ করা আছে সেগুলো বের হওয়ার পর শুধু প্রচ্ছদ দেখেই ফেলে রেখেছিল সে। ভেতরের পাতা উল্টে-পাল্টে পড়েনি কখনো। তখন হয়ত মানুষটি ছিল ঘরের মধ্যে। তার চিন্তা-ভাবনা, পরশ ও সান্নিধ্য তো পেয়েছিল। প্রয়োজন পড়েনি বইগুলো পড়ার। অতি নৈকট্য যে মানুষের কোনো কোনো গুণকে পর করে দেয়, আড়াল করে রাখে এটাই তার প্রমাণ। তাছাড়া ভাবের আদান-প্রদান সাক্ষাতে হলে ছাপা বই কষ্ট করে কেই-বা পড়ে? অথচ এক সপ্তাহের ব্যবধানে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম বলতে লেখাগুলোই একমাত্র বেকার অবলম্বন হয়ে আছে তার।
অনিকের হাতের মধ্যকার ম্যাগাজিনটা বের হয়েছে আজকেই। বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদক সাহেব অনেককে তাড়া দিয়ে কিছু লেখা যোগাড় করেন। যারা অনিকের বাবাকে সত্যিকারের ভালবাসতেন, তাদের কেউ কেউ স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের ব্যস্ততা থেকে কিছুটা সময় করে সম্পাদকের আহ্বানে সাড়া দেন। পুরোটাই তার বাবাকে নিয়ে লেখা। তার বাবার একটা শেষ লেখাও ম্যাগাজিনটার প্রথম পাতায় অন্তর্ভূক্ত আছে। সম্পাদক নিজে এসে অনিককে বিশেষ সংখ্যার এক কপি দিয়ে গেছে সংগ্রহে রাখার জন্য। বাবার শেষ স্থায়ী স্মৃতিটা পেয়েই ব্যালকোনিতে নিরিবিলি বসে নাড়াচাড়া করে দেখতে দেখতে কত কী যে ভাবছে সে এতক্ষণ!
ম্যাগাজিনে বাবার শেষ লেখাটা পড়তে গিয়ে অজ্ঞতার দরিয়া তার সামনে এসে বার বার ঢেউ তুলে যাচ্ছে। বাবার সাথে শেষ যোগাযোগের মাধ্যমটা অমোচনীয় দূরত্ব সৃষ্টি করছে। এটা ভাবতেই আবারও সে গুমরে কেঁদে ওঠে।
জন্মালে সবাই মরে—এটা এখনো ধ্রুব সত্য। কেউ কেউ তো জন্মের আগেও মরে। মৃত্যুর শোক ও বেদনা সময়ের সাথে সাথে প্রশমিত হয়। কিন্তু প্রিয় মানুষের জন্য কোনো কারণে আফসোস থাকলে সেটা সারা জীবন আগুনে দগ্ধ করে।
বাবা-মা অবশ্য কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন বাংলাটা শেখানোর। অনেক বাবা-মায়েই সেটা করে থাকেন। তাই অনিকের মতো অনেক ছেলে-মেয়েই বাংলাটা অন্তত বলতে পারে, শুনে বুঝতে পারে। কিন্তু বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধান ছাড়া বাংলা কেউ লিখতে ও পড়তে শেখে না।
প্রবাসে জীবন কঠিন ও সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আর কাছের মানুষ খুব একটা না থাকায় সংগ্রামটা আরো বেড়ে যায়। জীবিকা নির্বাহ ও সংসার সামলানোর পিছনে এত সময় যায় যে সেখানে সন্তানদের বাংলা পড়া ও লেখা শেখানোর মতো আলাদা কোনো কিছু করানোর সময় কোথায়? সেটা যদি আবার তেমন কোনো কাজে না লাগে। এই যে সময় হয় না, সময় হলেও ছেলে-মেয়েদের আগ্রহ থাকে না, সেটাই অনিকদের জন্য শেষে আফসোসের গভীর ছায়া হয়ে বাকি জীবন জুড়ে মনের নিভৃত একটা অঞ্চল স্যাঁতস্যাতে করে রাখে। সেখানে একাই হোঁচট খেয়ে পড়ে একাই উঠতে হয়। পড়ে যাওয়াটাও কেউ দেখতে পায় না। উঠতে সহায়তা করা তো দূরের কথা। যদিও তার পরবর্তী প্রজন্মের এ ব্যথা থাকবে না। থাকবে না আক্ষেপ। যে শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে সে শিকড়েও থাকবে না কোনো অবদান। হয়ত থাকবে কোনো এক সময়ে কৌতূহলবশত পূর্বপুরুষের ঐতিহাসিক জড় পাঠ।
লেখকের ছেলে বলেই অনিক সম্ভবত হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে এ অপূরণীয় ঘাটতি। সাধারণ প্রবাসীর সন্তান হলে সেটাও বোধ করত না সে। কারণ কোনো বৈষয়িক প্রয়োজনই নেই।
অনিকের জন্য তার উপলব্ধিজাত আফসোসের উপরি-পাওনাও আছে। সেটা হল তার এ বেদনা সে কাউকে বোঝাতে পারছে না। বোঝানো বলতে এ বেদনার সমব্যথী কাউকে খুঁজে পাওয়া। নিজের মানুষজন এবং অন্যান্যরা বার বার সান্ত্বনা দেবে বাবা হারানোর গভীর বেদনাকে প্রশমিত করতে। সময়ের সাথে সাথে সেটা প্রশমিতও হবে। কিন্তু তার যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিটাকে কেউ বুঝতে পারবে না। বোঝাতে গেলে শেষে হয়ত সবাই তাকেই ভুল বুঝবে।
সমব্যথী কাউকে এখানে খুঁজে পাবে না সে। পাওয়ার কথাও নয়। কারণ সে বড় হয়েছে ভিন্ন সাংস্কৃতিক আবহে, ভিন্ন ভাষায়। পাঁচ বছর বয়সে বাবা-মায়ের সাথে জন্মভূমি ছেড়ে সে লিখিত বাংলাটাকে সেখানেই সমাহিত করে রেখে এসেছে। এমনকি পরিণত বয়সে বিয়েও করেছে ক্রিস্টিনা নামের এখানকার এক মেয়েকে। বাঙ্গালি সংস্কৃতির তেমন কিছু জানে না সে। তাদের ঘরে এখন ষোল বছরের একটা চটপটে, শিক্ষিত তরুণী মেয়েও আছে। সেও গভীরে কিছু জানে না। জানার ফুরসতও নেই। প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়া এটা অর্জন করা যায় না। তাই তাদেরকেও বোঝানো যাবে না ঘাটতির এ মর্ম বেদনা। এছাড়া বন্ধুমহলের সবাই এ দেশের। সত্যিকারের গভীর অন্তর্গত কষ্টের সহমর্মী কেউ-ই হতে পারবে না।
মেয়ের নামটা অনিকের বাবাই রেখে দিয়েছিলেন। নামের অর্থ জিজ্ঞেস করলে বাবা জানিয়েছিলেন—শূন্য। তখন অর্থটা শুনে নামটা অনিকের একেবারে পছন্দ হয়নি। আজ মনে পড়ছে—বাবা, ঠিক নামই রেখেছিলেন। সে তো আসলেই পূর্বপুরুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে শিকড় বিচ্ছিন্ন একজন।
অনিক আবার পূর্বের প্রশ্নে ফিরে যায়। নিজেকে জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, আমাকে বাংলা লেখা শেখানোর ব্যাপারটা বাবা কি আগে ভেবেছিলেন? ভেবে থাকলে যথেষ্ট পদক্ষেপ নেননি কেন?
আবার নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজে—অবশ্য ছোটবেলায় দেখেছি তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন। মাও থাকতেন। হয়ত তারা চেষ্টা করেছিলেন তাদের সামর্থ্যের মধ্যে। কুলিয়ে উঠতে পারেননি। অবশ্য আমারও তো খুব আগ্রহ ছিল না। তখন কে জানত সেটাই এখন একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে?
‘সন্ধ্যায় বাবাকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান আছে। মনে নেই তোমার?’
কথাটি শোনামাত্রই হকচকিয়ে ওঠে অনিক। মাথাটা তুলতেই সামনে দেখে সত্যি বেলা গড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যা নামার বেশি সময় বাকি নেই। আর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে ক্রিস্টিনা পোশাক-আশাক পরে যাবার জন্য প্রস্তুত। তাদের মেয়েকে দেখতে না পেয়ে সে ক্রিস্টিনাকে জিজ্ঞেস করে,
-রিক্তা কোথায়?
-ও রেডি হচ্ছে। তুমি তাড়াতাড়ি করে রেডি হও। কখন থেকে ঝিম মেরে বসে আছ। অনুষ্ঠানে আগে আগে না গেলে সব ব্যবস্থা করবে কে? কত কাজ পড়ে আছে! বেশি সময় নিও না যেন।
তড়িঘড়ি করে ব্যালকোনির চেয়ার থেকে উঠে পড়ে অনিক। কিন্তু মাথায় তখনো এতক্ষণের চিন্তা-ভাবনার আবেশ রয়ে যায়। অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে, আর ভাবতে থাকে—যেতে হয় বলেই যেতে হবে। আনুষ্ঠানিকতা! এর পিছনেই জীবনের সব সময় চলে গেল। কাজের কাজ কিছুই হল না। যে ক্ষতির শিকার আমি তা কি আর পূরণ হবে? কী হবে লোক দেখানো অনুষ্ঠান করে?
প্রস্তুত হতে হতে মনের এ ভাবনা তাকে এতটা ধরে বসে যে শেষের প্রশ্নবোধক বাক্যটা নিজের অজান্তেই একটু জোরে বিড়বিড় করে বলতে থাকে। কথাটা শোনার সাথে সাথে ক্রিস্টিনা চিৎকার করে বলে ওঠে,
-কী বলছ এসব? অনুষ্ঠান করে কী হবে মানে? এতগুলো মানুষকে আসতে বলা হয়েছে! আর এখন বলছ ‘কী হবে?’ তোমার দায়িত্ব জ্ঞান যদি একটু থাকত!
-আমি কি বলেছি যে যাব না? দায়িত্ব পালন করব না? আমি বলছি—এসবের প্রয়োজনীয়তার কথা।
– নিজেদের একজন মানুষ চলে গেছে চিরদিনের জন্য। আর তাকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক কোনো অনুষ্ঠান হবে না?
অনিক জানে এ নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। অযথা সময় নষ্ট। ব্যথিতের ব্যথা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেই-বা বুঝবে? এত কিছু বুঝিয়ে কাজ নেই। উজানে সাঁতার কেটেও কাজ নেই। তার চেয়ে বরং ভাটির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াই ভাল। তাতে অন্তত বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হবে না। তবু একটু বিরক্তিবশত ক্রিস্টিনার কথায় রাজি হয়ে বলে,
-হবে, অবশ্যই হবে।
তাদের উচ্চবাচ্য শুনে রিক্তা চলে আসে। তাকে দেখে অনিক শুধু বলে ওঠে,
-চল, আমিও রেডি।





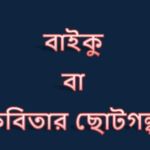

Be the first to comment